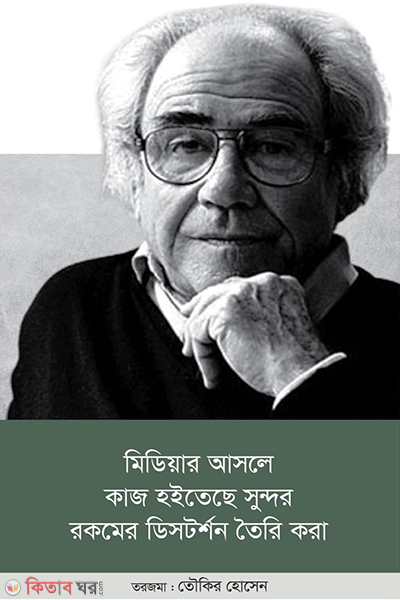
ইন্টারভিউ-ফিলোসফি ২ (জঁ বদ্রিয়া)
বদ্রিয়ারে পড়া’র রিস্ক বদ্রিয়ারে পড়া একধরণের রিস্ক নেয়া। আপনি চাইলে নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন। জ্য বদ্রিয়া, ফরাসি দার্শনিক, যার সিমুলেশন-সিমুলাক্রামের রেফারেন্স আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া আর অটোমেশনের যুগে হরদম টানা হয়, তার এই ইন্টারভিউগুলা “ফরগেট ফুকো”-নামের বইয়ে ১৯৭৭ সালে পাবলিশ করা হইছিল। অবশ্য তার আগে প্রায় নয় বছর আগে বদ্রিয়ার পিএইডি থিসিস “সিস্টেম অফ অবজেক্টস” পাবলিশ হয়, ১৯৬৮ সালে- সেইখানে তিনি অবজেক্টসের সিস্টেমের এনালাইসিস করছিলেন মডার্ন কনজুমার সোসাইটিরে সামনে রেখে। সিস্টেম, অবজেক্টস, মিডিয়া এইসব থেকে বদ্রিয়া গেছেন এরপরে আরও নানা জায়গায়, ইল্যুশনস, কনজুমারিজম, যুদ্ধসহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষায় বদ্রিয়া পরিচিত না। পরিচিত না হওয়ার কারণে বদ্রিয়ারে ভুলভাবে ইন্টারপ্রেট করবার অনেক সুযোগ আছে। আর ইন্টারভিউ যেহেতু কনটেক্সট ধরে আসে না, এইখানে এই আশংকা আরও বেশি। এই কারণে, বদ্রিয়া পড়াটা একধরণের রিস্ক। আর বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ফিলোসফি, দর্শনচর্চার হালহাকিকত খুব করুণ, শোচনীয়। সামাজিকভাবে অত্যাচারিত হইতে হইতে এখন প্রায় মৃতপ্রায়। বাংলায় ফিলোসফির এই মরণের পিছনে নানাবিধ কারণ আছে। প্রথমত, আমাদের দেশের যে কয়টা জ্ঞান-উৎপাদনকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাতে ফিলোসফি/দর্শন কখনোই মৌলিক পাঠ হিসাবে বেড়ে উঠতে পারে নাই। এর কারণ আছে। তবে উন্নতবিশ্বে ফিলোসফি যে খুব উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে তাও কিন্তু বলা যাবে না। ফিলোসফি পড়ে গ্র্যাজুয়েট হলে অটোমেশনের যুগে চাকরির কোন নিশ্চয়তা নাই কিন্তু। আবার গুটিকয়েক ফিলোসফার যাদেরকে আমরা বেশি করে চিনি, তারা যে একটা বড় সোসাইটিকে প্রতিনিধিত্ব করে তাও কিন্তু না। যে কারণে লেইড-ব্যাক বা আর্মচেয়ার ফিলোসফার নামক গালি চালু আছে, এবং পোস্টমডার্ন ফিলোসফারদের ক্ষেত্রে যা আরও বেশি করে শোনা যায়, ফিলোসফারদের কাজ কেবল একাডেমিক গেইম খেলা, নাথিং এলস। বিভিন্ন মিনিং, হাইপোথিসিস তৈরি করে এমন এক অ্যাবস্ট্র্যাকশনের দুনিয়ায় তারা হারায়ে যান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা রিয়ালিটিরেও ছাড়ায়ে যায়। উন্নত বিশ্বে এই ধরণের সমালোচনা থাকলেও, ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু সেই সমালোচনার ধার ধরে ফিলোসফিকে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয় নাই। কারণ, সেই এগারশ বারশ শতাব্দী থেকে চলে আসা যে জ্ঞানের সিলসিলা সেই পরিক্রমায় ইউনিভার্সিটিগুলো ঠিকই জানে, কোনও বিষয়ে স্পেশালিস্ট/একাডেমিক/এক্সপার্ট বাইর করতে হলে তার শুরুতেই জ্ঞানের একদম বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে। এবং সেই বেসিক আদতে ফিলোসফিরই বেসিক পাঠ। তাই নানাবিধ সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও সোশ্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স, সায়েন্স কোন জ্ঞানকান্ডেই আমরা থিওরি ছাড়া আলাপ হতে দেখি না। এবং এই থিওরির পিতা-মাতারা মূলত বিজ্ঞানী, দার্শনিকেরাই। তবে একাডেমিয়ার পিতা-মাতা দার্শনিক হলেও তাদের যে ক্রিটিসাইজ করা যাবে না, এমন কিন্তু নয়। একাডেমিয়ার পিতা-মাতার জ্ঞানেভাবে অনেক তত্ত্ব কপচাতে পারেন আবার একইসাথে রাজনৈতিকভাবে কোন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আবার রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হতে পারেন। মাঝেমধ্যে এই ঘুঁটি হওয়ার অভ্যাস বদ্রিয়ার ভাষায় চরমে পৌঁছে যায়- বাংলাদেশ তার সেরা একটি উদাহরণ।
এইখানে রাজনৈতিকভাবে আমলাতন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে, সামাজিকভাবে স্বীকৃত মতাদর্শের বাইরে নতুন কিছু করা কঠিন। সেই অর্থে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ আসলে একটি কনজার্ভেটিভ রাষ্ট্রব্যবস্থা। শক্তিশালী সমাজ, শক্তিশালী আমলার বাইরে গিয়ে ফিলোসফি বেশি টিকতে পারে নাই। তাই দর্শনচর্চা শেকড় হারাইছে। বাংলা ভাষায়, দেশি ধরণের ফিলোসফিও গড়ে উঠতে পারে নাই। এর কারণ গড়ে উঠবার যে সকল ফ্যাক্টর থাকা লাগে, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, ভাষার ব্যবহারযোগ্যতা তার কোনটাই আমাদের দার্শনিকগণ দিতে পারেন নাই।
তাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা খুব লিনিয়ার-গড়ে চলেছে। আহমদ ছফা, আব্দুর রাজ্জাক, সলিমুল্লা খান- এরকম সিলসিলা কিংবা গুটিকয়েক পশ্চিমা পোস্টমডার্ন প্রবেশিকা বা লালন শাহের কাব্যিকতা, জীবন-দর্শন- খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আধা-বিকশিত হওয়ার কারণে নাই আলাদা কোন চিন্তার প্রতিষ্ঠান, নাই শক্তিশালী একাডেমিয়া (দার্শনিকদের জায়গা যেখানে আমলারা নিছে)। এর ফলে সম্মিলিত দর্শনচর্চার অভাব এখনও মেটানো যায় নি। সম্মিলিত চিন্তাভাবনার অভাবে যেইটা ঘটছে- এক নয়া ঢাকাই এস্থেটিসিজমের উৎপত্তি। যেইখানে সেকেলে হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক সংগঠনগুলো স্রেফ ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য কিছু জার্গন মুখে তুলে নেয়, আর রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হয় (অটোনোমিয়া মুভমেন্টের ধারেকাছেও নেই সেইসব আন্দোলন)। কিংবা ঢাকা শহরে এক নতুন ট্রেন্ড- মানুষজন পাগলের মতো এখন ইন্টেলেকচুয়াল হইতে চায়, এর কারণ কিন্তু বদ্রিয়াই ভালো বইলা গেছেন। যখন আপনি একটা স্পেসে ভ্যাকুয়াম তৈরি করেন, সেখানের জড়তার কারণে ব্ল্যাকহোলের মতো আশপাশের সবকিছুরে আপনি টাইনা নিয়া আসতে থাকবেন। ইন্টেলেকচুয়াল ব্ল্যাকহোলে তাই আমাদের এই ঢাকাই নিউ জেন এখন পাগলের মতো ইন্টেলেকচুয়াল হইতে চাইতেছে। যদিও তারা জানে না আসলে এই বালটা কী। কিছু জার্গন সম্বল করে, ট্রাই করে ইন্টেলেকচুয়াল হইতে। দু:খের ব্যাপার বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিতা, ইন্টেলেকচুয়ালিটির কোন মিনিং-ই আর অবশিষ্ট নাই। সিমন দ্য বোভোয়ার সেই কথা, যখন কোনকিছু থাকে না যা থাকে তা কেবল নস্টালজিয়া। নস্টালজিয়ার উপর ভর করে আমাদের এই জেনারেশন “ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার স্বপ্ন” ডেকে আনবার ট্রাই করে। কিছু প্রতিষ্ঠানও দাঁড়ায়ে যায় তরুণদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ও স্বপ্ন দেখাবার। প্রতিষ্ঠানগুলো স্বপ্ন দেখাতেও পারে তবে সেই স্বপ্ন-বিজ্ঞান-ইন্টেলেকচুয়ালিটি সবকিছুরই মিনিং মিলেমিশে একাকার হইয়া কোনকিছুরেই আর আলাদা করে চিনা যায় না।এই কারণে জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে বাংলা ভাষায় ফিলোসফির কোন আকার নাই, তেমনি রিয়ালিটি চেক দিলে দেখা যায়, বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চারও কোন মানে নাই। অতএব, আপনি ডেফিনিটলি বইটা পড়তেছেন মানে একটা রিস্ক নিতেছেন।
- নাম : ইন্টারভিউ-ফিলোসফি ২ (জঁ বদ্রিয়া)
- লেখক: জঁ বদ্রিয়া
- অনুবাদক: তৌকির হোসেন
- প্রকাশনী: : বাছবিচার বুকস
- পৃষ্ঠা সংখ্যা : 56
- ভাষা : bangla
- বান্ডিং : paperback
- প্রথম প্রকাশ: 2023













