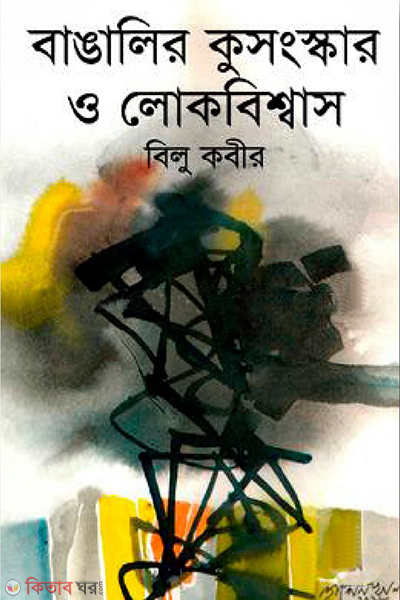
বাঙালির কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাস
যে জাতির পৌরাণিক জগৎ যত প্রসারিত, যে জাতির মিথ-আকাশ যত নাক্ষত্রিক, যে জাতির কিংবদন্তি মায়া-ব্রত-প্রথা যত সমৃদ্ধ সেই জাতির কুসংস্কার এবং লোকবিশ্বাসের অনুশীলন ও সাহিত্য তত বেশি সম্পদশালী। সেই বিবেচনায় সাগরপাড়ের বাঙালি জাতির কুসংস্কার আর লোকবিশ্বাসের প্রসারিত জগৎ দেখে গৌরব বোধ করার কারণ রয়েছে। তাদের জাগতিক এবং প্রাযৌক্তিক জ্ঞান-ঘাটতির সূচক হিসেবে এই কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের যে গুরুত্বপূর্ণ আকরমূল্য রয়েছে, বিষয়টি কেবল বাঙালিদের মানসকাঠামোর দারিদ্র্যই প্রমাণ করে না, তা-সব সেই যাবতীয় শেকড়-অতীতের সূত্রসংবাদ দেয় যে, এই জাতি কত ধরনের প্রতিকূলতার সাথে লড়ে-যুঝে আজ একটি সংস্কৃতিপ্রবণ ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান নির্মাণ করেছে।
সহস্রকালের পালনে-অনুশীলনে, অনাদরে-অবিশ্লেষণে নিজেদের কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসগুলো বাঙালির গা-সওয়া সাধারণ। কিন্তু প্রায়শই এইসব বিষয়-ধুন্দুমার অর্থহীন মনে হলেও এর পটভূমিতে যে অভিজ্ঞতা, বিপর্যয়, ত্রাণপ্রত্যাশা এবং আনন্দ-বেদনার পঙ্ক্তি রয়েছে, বিশ্লেষণের আলো ফেলতে হবে সেইসব অন্ধকারের ওপর। সেই আলোকসম্পাতের কাজটি এখন যে পরিমাণে করা হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু ভবিষ্যতে যে এর ব্যাপক হিসাব-নিকাশ হবে, তাতে সন্দেহ কী? কিন্তু সেই গবেষণার কাজটি যারা করবেন, তাদের মূল উপাদানগুলোতো সংগৃহীত থাকা দরকার। নইলে কী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিটা হবে? প্রশ্ন না? নিশ্চয়ই। এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা জিজ্ঞাসা বটে। সেই কাজকে এগিয়ে নিতে, সেই উত্তরকালের লোকগবেষকদের যোগালি হিসেবে কিছু কাজের অগ্রিম যাত্রাসরূপ এই আয়োজন। যদি কাজে আসে তো ভালো, না আসলে কী আর বলব? সেও ভালো। কিন্তু পুরোটাই আবর্জনা হবে তা নিশ্চয়ই নয়।
২. কুসংস্কার এবং লোকবিশ্বাস, বিষয় দুটি যেসব বাংলা বিষয় ও শব্দের সাথে সম্পর্কিত, তা হলো : অজ্ঞান, অবিবেক, মোহ, মূর্খতা, অজ্ঞতা, সারল্য, সন্দেহ, হাতুড়েবিদ্যা, দৈব, ভাগ্য, অদৃষ্ট, শূন্যবাদ, মায়া, সম্মোহন, সংকীর্ণতা, মানসদারিদ্র্য, পূর্বধারণা, গোঁড়ামি, মুগ্ধতা, বিশ্বাস, দুর্বলতা, মনোসমর্থন, রূপকথা, লোকভয়, সন্দেহ, সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা, সংশয়বাদ, স্বপ্নকথা, কেচ্ছা-কাহিনি, পুরাণ, মিথ, কিংবদন্তি, প্রবাদ, প্রবচন, জনশ্রুতি, ব্রতকথা, খনা, ডাক, ধর্ম, ভয়, মন্ত্র, ভৌতিকত্ব, প্রথা, অন্ধবিশ্বাস, জড়বাদ, দেবদেবী, দৈত্য, ভূতপ্রেত, জাদু, ধর্মীয় কুসংস্কার, কথিত, অকথিত, সংস্কার, গালগল্প, আন্দাজ, প্রচলন, প্রথা ইত্যাদি। এইসব বিষয়-বস্তু-ভাব বাঙালির কুসংস্কার এবং লোকবিশ্বাসের ওপর জোরালো প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। তাই আলোচ্য শব্দ এবং তা-সবের ব্যুৎপত্তিগত কার্যকারণকে বাঙালির অন্তর্বৈশিষ্ট্যের সাথে সংহত করে গভীর চিন্তা করলে মনে হয়, এই জাতির ভাবকল্প, কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি এবং পালন-পার্বণের নিগূঢ় যুক্তি ও সত্যটির হদিস মিলতে পারে। কারণ বিষয়গুলো একটার সাথে অন্যটি সম্পর্কিত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একটি অন্যটি থেকে উৎসারিত, একটি অপরটির পূর্বশর্ত। একটি আরেকটিকে আমলে আনার সুফল কিংবা কুফল, এমনকি কোনো কোনোটি কোনো কোনোটির পরিপূরকও। ভাবলে অনুধাবন করা যাবে যে, শব্দগুলো একটির সাথে অন্যটি লাগোয়া, এই লাগোয়া বাস্তবতাটি অর্থ, উচ্চারণ এবং ভাব ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই।
৩. এই গ্রন্থটি রচনা করার ক্ষেত্রে লাইব্রেরি ওয়ার্ক করা হয়েছে অকিঞ্চিৎকর পরিমাণে। সামান্য মাত্রায় যেসব বইপত্রের সাহায্য নিয়েছি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সাথে সাথে তার তথ্যায়ন করা হয়েছে। এতে সিংহভাগ ভুক্তি আমার পার হয়ে আসা জীবনপরিসর থেকে কুড়িয়ে একীভূত করা। সেই বাস্তবতায় এমন দাবি যুক্তিযুক্ত হবে যে, এটি সর্বৈবভাবেই একটি মৌলিক কাজ। যার ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি সমগ্র জীবনের পথেপ্রান্তরে। এসব বিষয়-পালন বাঙালির সাধারণ যাপিত জীবনের সাথে এতোটাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত যে, এর সন্ধান করতে আলাদা করে আর ঘর থেকে মাঠে বের হতে হয়নি। বরং সারা পথের ক্লান্তি সংগ্রহের খাতায় এগুলোর ক্রমপুঞ্জীভূত সসুদ মুনাফাসহ আসল বা সাহিত্যের মূলধন হিসেবে বিনিয়োজিত হয়েছে। অতএব, ‘চিনলে জরি/না চিনলে বনের খড়ি’। হয়তো গড়সাপটা ঝিনুক কুড়িয়েছি, এখন যিনি যতটা মুক্তা আহরণ করতে পারেন। কিন্তু তেমন কোনো পাকা জহুরির হাত যদি পড়ে, তাহলে এমনও তো হতে পারে যে, যা কুড়িয়েছি সবই মুক্তা, কোনোটাই মামুলি নুড়ি নয়। ঝিনুকের খোলস বলতে কোনো বর্জ্য নেই সেখানটায়। মানে সবমিলিয়ে আমার স্বপ্ন আকাশছোঁয়া। এসব বিষয় নিয়ে যে কাজ করতে পারিনি বা পারি না, সেই কাজ অন্যরা পারবেন ভেবেই তাদের কাজকে কিছুটা এগিয়ে রাখা। আর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা।
৪. এই বইটিতে নেই নেই করে ৪৯২টি ভুক্তি আছে। নানান তাদের ধরন, বিচিত্র তাদের বিষয়-মর্তবা। কাজটি করতে গিয়ে ধর্মসংশ্লিষ্ট কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, মিথ, লোক-অলোক, পরস্তাকে যদ্দূর পারা গেছে বর্জন করেছি। পাছে কেউ ভুল বুঝে তার সংবেদনশীল নরমে আঘাত পান। সাহস পাইনি ব্যাপারটি পুরোপুরি তা নয়, বরং এড়িয়ে গেছি। বিষয়টি সিংহভাগ ক্ষেত্রে সেই রকমই। নইলে আরও পাঁচ শ’র অধিক ভুক্তি এই গ্রন্থের কলেবরকে দশাসই করতে অবশ্যই পারতো। এবং সেটা করা গেলে বইটিতে অনেক বেশি সমৃদ্ধি ঘটত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইচ্ছা এবং সম্ভবত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেটা পারিনি, করিনি। কুণ্ঠা কাটিয়ে স্বীকারই করি, আমার অন্তত এখনও ভয়ই করে। ‘সাহস না হওয়া’ আর ‘ভয় করা’কি একই কথা? যদি তা-ই হয়, তাহলে তা-ই। লজ্জিত। বাকি কাজ অন্য কেউ করবেন। মিথ্যা বলার চেয়ে সত্যকে চেপে যাওয়া নিদেনপক্ষের সততাতো বটেই। ভীতু অসহায়ের জন্য সেই খড়কুটোইতো অবলম্বন। যিনি বা যারা. আমার চাইতে সাহসী এবং কর্তব্যপরায়ণে আপসহীন। সেই কাক্সিক্ষত উত্তরপ্রজন্মের পথ চাইতে চাইতে অনেকটা চলে যাওয়া।
৫. আমার জন্য যা শিল্প, পাঠকের জন্য যা সংস্কৃতি, প্রকাশকের জন্য তা শিল্প-সংস্কৃতির সাথে যুগপৎভাবে বিনিয়োগও। যেখানে আসলই ওঠে কিনা, সেখানে তাকে মুনাফা করতে হবে। তো এই রকম একটা বই প্রকাশ করতে প্রকাশকের সাহস দেখে বাঁচি না। জয়তী’র কর্ণধার প্রিয়ভাজন মাজেদুল হাসান এই বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকেতো বটেই, বুঝিবা পাঠকদেরকেও ঋণী করলেন। নিজেকে নিয়েতো নিজেই উচ্ছ্বসিত হওয়া চলে না, তবু বলি, এ জন্য হয়তো বাংলাসাহিত্য তাকে এবং তার প্রতিষ্ঠানকে মনে রাখবে, ভালোবাসবে। বইটির নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। চূড়ান্ত পর্যায়ে আমারতো সেই একই অভ্যাস, শেষ ভরসা প্রিয় পাঠক। তারা কি বলেন, কিভাবে নেন বইটিকে। অপেক্ষায় রইলাম। সকলের কল্যাণ হোক। ধন্যবাদ।













